পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা প্রশ্ন উত্তর
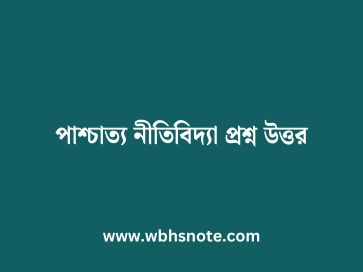
1. মানুষের দুটি অস্তিত্ব কী কী?
মানুষের অস্তিত্বের দুটি প্রকার
নীতিবিদ্যার আলোচনায় আমরা সমাজবদ্ধ মানুষের অস্তিত্বের দুটি দিকের সন্ধান পাই। যথা- দৈহিক অস্তিত্বের দিক এবং আদর্শগত বা মূল্যবোধের দিক।
(1) দৈহিক অস্তিত্বের দিক: মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব হল তার বাস্তব অস্তিত্ব, যেখানে সে তার দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য বিবিধ আবশ্যিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এখানে সে খাদ্য, জল ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে বেঁচে থেকে, জীবনযাপন করে।
(2) আদর্শগত অস্তিত্বের দিক: মানুষের আদর্শগত অস্তিত্বের দিকটি হল সেই দিক যেখানে মূল্য বা আদর্শের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের অর্থ ও পূর্ণতাকে খুঁজে পায়। খাদ্য, জল ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে জীবনধারণ করা জীবনের প্রকৃত অর্থ নয়। জীবনের প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছে আদর্শের মধ্যে, মূল্যবোধের মধ্যে। এই আদর্শ বা মূল্যের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায় বলেই সে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র।
2. নীতিবিজ্ঞানকে নীতিদর্শন বলা হয় কেন?
নীতিবিজ্ঞানকে নীতিদর্শন বলার কারণ গুলি নিম্নরূপ-
- প্রথমত: নীতিবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মত বর্ণনামূলক নয়। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের বর্ণনা করে না, তার মূল্যায়ন করে। নৈতিক আদর্শের মানদণ্ডে নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণ ভালো না মন্দ, ন্যায় না অন্যায় তা বিচার করে।
- দ্বিতীয়ত: নৈতিক আদর্শ প্রত্যক্ষজাত বিষয় না হওয়ায় বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতি এক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। দর্শনের বিচার- বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এখানে আশ্রয় করতে হয়।
- তৃতীয়ত: দর্শনকে অনুসরণ করে নীতিবিদ্যা পরম আদর্শ সম্বন্ধে নৈতিকতার মৌল প্রশ্নগুলি তোলে। ম্যাকেঞ্জি এ প্রসঙ্গে বলেন, নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার একটি দিক মাত্র নয়।
এই কারণে নীতিবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ‘Moral Philosophy’I ‘Moral’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘Mores’ থেকে। ‘Mores’ শব্দটির অর্থ হল রীতিনীতি বা অভ্যাস। নৈতিক নিয়মগুলিকে বলা হয় ‘Moral law’। এই নিয়মগুলি সার্বিকভাবে প্রযোজ্য হয়। সামগ্রিক এবং সার্বিকতা এই বৈশিষ্ট্য গুলির জন্য নীতিবিজ্ঞানকে নীতিদর্শন বলা হয়।
3. নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
নীতিব্যিদার সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায় সেগুলি নিম্নরূপ-
- প্রথমত: নীতিবিদ্যা এক ধরনের বিজ্ঞান। যে-কোনো বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি নীতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। প্রতিটি বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে। বিজ্ঞান সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও নিরপেক্ষ জ্ঞান দিয়ে থাকে। নীতিবিদ্যাও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুচিন্তিত, সুশৃঙ্খল জ্ঞান দেয়।
- দ্বিতীয়ত: বিজ্ঞান হিসেবে নীতিবিদ্যা হল আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। এমন কতগুলি বিজ্ঞান আছে যেগুলি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান, সেগুলি বর্ণনামূলক। বস্তুটি বা ঘটনাটি বাস্তবে যেমন তারই বিবরণ দেওয়া এই বিজ্ঞানের কাজ। যেমন- রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি। অপরপক্ষে নীতিবিজ্ঞান হল আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। আদর্শের মানদণ্ডে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে নীতিবিজ্ঞান।
- তৃতীয়ত: নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের আচরণ বলতে বোঝায় যাবতীয় স্বেচ্ছাকৃত কাজের সমষ্টিকে। শিশুর আচরণ, জড়বস্তু, উন্মাদ ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণকে নৈতিক ক্রিয়া বলা যায় না।
- চতুর্থত: নীতিবিদ্যা সামাজিক মানুষের আচরণের ভালোত্ব-মন্দত্ব, ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।
4. নৈতিকতার প্রকৃতি আলোচনা করো।
নৈতিকতা বা Morality হল নীতিবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়। নৈতিকতার প্রকৃতি নিম্নরূপ-
- মানুষের আচরণের মাধ্যমে নৈতিকতার প্রকাশ ঘটে। একজন ব্যক্তির থেকে নৈতিকতা অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।
- নৈতিকতার ধর্ম হল সর্বজনীন নৈতিক বিধিগুলির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।
- জীবনে চলার পথে এই পরম মূল্যবান নৈতিক বিধিগুলি আমাদের কর্তব্যকর্ম স্থির করে দেয়।
- নৈতিকতা যুক্তিনির্ভর ও মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত।
- নৈতিকতা হল বিবেকের অনুশাসন বা আদেশ।
5. নৈতিকতার প্রশ্নে সক্রেটিসের ভূমিকা কী?
নৈতিকতার প্রশ্নে সক্রেটিসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আদর্শগত এবং প্রশংসনীয়। সক্রেটিস ছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর গুরু। তাঁর কোনো লিখিত গ্রন্থ আমরা পাইনি। কিন্তু তাঁর শিষ্য প্লেটোর বিভিন্ন সংলাপে আমরা তাঁর আলোচনা পাই। সেসব সংলাপের মধ্যে অন্যতম হল ‘ক্লিটো’ (Crito) নামক সংলাপটি।
বিশিষ্ট নীতিবিদ উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কেনা তাঁর ‘Ethics’ নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন, প্লেটোর সংলাপ ক্রিটোর ভূমিকায় আমরা সক্রেটিসের সততা এবং ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাই। সেখানে প্লেটো সক্রেটিসকে একজন নৈতিকতার পৃষ্ঠপোষকরূপে আখ্যা দেন। কেন-না তিনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কারাগার থেকে পলায়ন করেননি এই নৈতিকতার জন্যই। নৈতিকতার জন্যই তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতেও কোনো দ্বিধা করেননি। কাজেই, নৈতিকতার প্রশ্নে সক্রেটিসের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম।
6. সক্রেটিসের নৈতিক চিন্তার দৃষ্টান্তটি লেখো?
মহামানব সক্রেটিস নৈতিকতাকে মানব জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করেছেন। দেশদ্রোহীতার মিথ্যা অভিযোগে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলেও কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করার সুযোগ সক্রেটিসের কাছে ছিল। কিন্তু তাঁর নীতিবোধ তাঁকে কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্বিঘ্নে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসৎগুণের সঙ্গে আপোষ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই আদর্শ নামক সৎগুণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে মৃত্যুদণ্ডকে সাদরে গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি নৈতিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নৈতিকতাকে মানবজীবনের পরম আদর্শরূপে গণ্য করে সক্রেটিসের নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে চির অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
7. নৈতিকতার সমর্থনে সক্রেটিসের যুক্তি কী?
নৈতিকতার সমর্থনে সক্রেটিসের যে যুক্তি সেটির তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। এই যুক্তি ছিল আইন ভঙ্গ করে পালানো উচিত নয় কেন- তার পক্ষে।
- প্রথমত: তিনি যদি পলায়ন করেন তবে রাষ্ট্রের আইনকে অসম্মান করা হবে এবং রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করা হবে।
- দ্বিতীয়ত: কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করার অর্থ হল সেই রাষ্ট্রের আইনের প্রতি অনুগত থাকার নীরব সম্মতি। তাই পলায়ন করলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে যে চুক্তি, সেই চুক্তি ভঙ্গ করা হবে।
- তৃতীয়ত: সমাজ বা রাষ্ট্র হল কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতা বা শিক্ষক তুল্য। আর ব্যক্তির উচিত তার পিতা-মাতা ও শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করা।
8. নীতিবিদ্যা হল একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।’- ব্যাখ্যা করো। অথবা, নীতিবিদ্যাকে কি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
নীতিবিদ্যা হল একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Normative Science)। আদর্শ বলতে বোঝায় যা বাস্তবে ঘটে না, কিন্তু যা ঘটা উচিত। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানে যে-কোনো একটি আদর্শের প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মানবজীবনের মূলত তিনটি আদর্শকে সত্য, শিব (মঙ্গল বা কল্যাণ) ও সুন্দরকে পরম আদর্শ (Summum Bonum) বলা হয়। এই তিনটি পরম আদর্শের উপর ভিত্তি করে যুক্তিবিজ্ঞান (Logic), নীতিবিজ্ঞান (Ethics) ও সৌন্দর্য বিজ্ঞান (Aesthetics)- এই তিনটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান গঠিত হয়েছে। ‘শিব’ বা ‘কল্যাণ’ কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করে এবং সেই আদর্শকে জেনে তার স্বরূপ নির্ণয় করে। কাজেই, নীতিবিদ্যা হল একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
9. আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় যে তিন ধরনের তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় সেগুলি কী কী?
আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার তত্ত্বসমূহ
আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় তিন ধরনের তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথা- কর্তব্যবাদ (Deontology), পরিণামবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ (Consequentialism or Teleology) এবং সগুণের নীতিতত্ত্ব (Virtue Ethics)
(1) কর্তৃব্যবাদ : কর্তব্যবাদ বলতে আমরা সেই কর্মনীতিকে বুঝি যেখানে কর্তব্যতার নিরিখে কোনো কাজের নৈতিক মূল্য নিরূপণ করা হয়। নিছক ফলাফল নয়, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য আমাদের কর্মনীতি হওয়া উচিত।
(2) পরিণামবাদ: পরিণামবাদ অনুসারে কোনো কর্ম ন-নৈতিক (Non- moral) ফলাফল উৎপন্ন করে বা করতে পারে তার নিরিখে সেই কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।
(3) সগুণের নীতিভত্ত্ব: সদগুণের নীতিতত্ত্ব অনুসারে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কাজ বা কর্মনীতির পরিমাণ বা কর্তব্যতা বিচারের পরিবর্তে ব্যক্তির চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অ্যারিস্টটলের Virtue Ethics -এর উপর ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীতে নীতিতত্ত্ব নতুন জীবন লাভ করেছে এবং উপযোগবাদ ও কর্তব্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।
10. টীকা লেখো: ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া।
ঐচ্ছিক ক্রিয়া
যেসব ক্রিয়া মানুষের স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ যেসব ক্রিয়া করা বা না করার স্বাধীনতা আমাদের অছে; সেসব ক্রিয়াই ঐচ্ছিক ক্রিয়া। এই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক বিচার, ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং এই ধরনের ক্রিয়াই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। যেমন-চুরি করা, অপরকে আঘাত করা, অপরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি ক্রিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়া।
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়। কেন-না, এসব ক্রিয়ার নৈতিক বিচার, ভালো-মন্দ বিচার হয় না। যেসব ক্রিয়া মানুষের স্বেচ্ছাধীন নয় অর্থাৎ যেসব ক্রিয়া করা বা না করার উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সেইসব ক্রিয়াই হল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। যেমন- শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, হাঁচি, কাশি, রক্ত সঞ্চালন ইত্যাদি ক্রিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া।
11. ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে কেন নৈতিক বলা হয়?
ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে নৈতিক বলা হয়। কারণ ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলতে আমরা সেই ক্রিয়াকে বুঝি যার উপর আমাদের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ থাকে। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ যার ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আছে তার দ্বারা যখন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন তা ঐচ্ছিক ক্রিয়ারূপে গণ্য হয়। এইরূপ ক্রিয়া সে আবেগের তাড়নায় সম্পন্ন করে না। ব্যক্তি তার জ্ঞাতসারে বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করে। লক্ষ্য এবং উপায়ের ক্ষেত্রে তার অগ্রদৃষ্টি এবং নির্ধারণের ক্ষমতা থাকে। এইরূপ কাজের জন্য কোনো ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে দায়ী করা যায়।
12. নৈতিকতার বিষয়টি মানুষের কোন্ বোধ থেকে উঠে আসে?
সমাজবদ্ধ মানুষ তার দৈহিক অস্তিত্বের সীমায় কখনোই সীমায়িত হতে পারেনি। খাদ্য, জল, বাতাস ইত্যাদি গ্রহণ করে জীবনধারণের মাধ্যমে মানুষ কখনোই তার জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই মানুষ তার দৈহিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করে মহত্তর কোনো বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়েছে যেখানে সে তার জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। এই অতিক্রমণের ফলস্বরূপ মানুষ আদর্শ বা মূল্যবোধের স্তরে উপনীত হয়েছে এবং অস্তিত্বের এই আদর্শ বা মূল্যবোধের স্তরে মানুষ তার জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেছে।
এই আদর্শ বা মূল্যবোধের জন্যই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্বশীল করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। আদর্শ বা মূল্যবোধ রক্ষার্থে সক্রেটিসের প্রাণত্যাগ তাই আজও উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই আদর্শ বা মূল্যবোধ মানুষের জীবনের মূল মন্ত্র যা তাকে চির অবিস্মরণীয় করে রাখে। নৈতিকতার বিষয়টি মানুষের এই আদর্শ বা মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত।
আরও পড়ুন – মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা প্রশ্ন উত্তর