জন লকের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় দাও
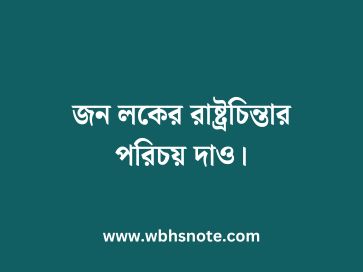
প্রকৃতির রাজ্য
জন লক তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে প্রাক্-রাষ্ট্রীয় জীবনে এক প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) -এর বর্ণনা করেছেন, যেখানে প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) ও প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় মানুষের জীবন ছিল সহজ ও স্বাভাবিক; সমাজ ছিল সাম্যবাদী। সকলেরই সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল। সর্বত্র বিরাজ করত শান্তি ও শৃঙ্খলা। স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ ছিল না, প্রাধান্য দেওয়া হত যুক্তি এবং বিচারকে। তবে কালের নিয়মে, প্রকৃতির রাজ্যে নানা সংকট উপস্থিত হয়। সম্পত্তির অধিকার ভোগ করাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পায় বৈষম্য। লকের মতে, মূলত ৩টি কারণে প্রকৃতির রাজ্যে অশান্তি বিরাজ করত, সেগুলি হল-
- আইনব্যবস্থার অভাব: মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে কোনও আনুষ্ঠানিক আইনব্যবস্থা ছিল না।
- নিরপেক্ষ বিচারকের অভাব: বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃতির রাজ্যে কোনও নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন না।
- সর্বমান্য প্রাধিকারীর (Authority) অভাব: প্রকৃতির রাজ্যে বিচারকের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য ছিল না কোনও নির্বাহী ব্যবস্থাও।
এই সকল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে মানুষ চুক্তির পথে পা বাড়ায় এবং গড়ে তোলে গণসমাজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।
চুক্তি মতবাদ
লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক সমাজ গঠনের জন্য দুটি পর্যায়ে চুক্তি করেছিল। সাধারণত এই দুটি চুক্তি- সামাজিক চুক্তি ও সরকারি চুক্তি নামে পরিচিত।
- সামাজিক চুক্তি: প্রথম চুক্তিটি হয়েছিল প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের নিজেদের মধ্যে। এই চুক্তির ফলেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এই চুক্তিটিকে সামাজিক চুক্তি (Social Contract) বলা হয়।
- সরকারি চুক্তি: দ্বিতীয় চুক্তিটি হয়েছিল মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রশাসকের বা শাসকের সঙ্গে শাসিতের। এই চুক্তিতে বলা হয় শাসক যদি অপশাসন করেন, তবে সাধারণ প্রজারা তাঁকে পদচ্যুত করতে পারবে। এই চুক্তিটি সরকারি চুক্তি (Governmental Contract) নামে পরিচিত।
লকের মতে, চুক্তির পর প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির কাছে যেসকল অধিকারসমূহ সমর্পণ করেছিল, তা হল- আইন প্রণয়নের অধিকার, প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের অধিকার এবং আইনভঙ্গকারীর অপরাধের বিচার করার অধিকার। তবে এমন কিছু অধিকারও ছিল, যা প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ রাষ্ট্রশক্তির কাছে সমর্পণ করেনি, যেমন- ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার।
সার্বভৌমিকতা
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে লক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি, তবে একেবারে যে নীরব ছিলেন তাও নয়। তিনি বলেছেন যে, রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতার জোরে অবাধ ও যথেচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী নয়। কারণ, সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হল জনগণ। তারাই রাষ্ট্রের কাছে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছিল। লকের তত্ত্ব অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতাকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা- আইনগত সার্বাভৗমিকতা: এখানে রাষ্ট্রের আইনসভা আইনগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং রাজনৈতিক সার্বাভৗমিকতা: এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় জনগণ।
সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থা
(i) জনগণের সম্মতি
লকের মতে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ চুক্তির মাধ্যমে যাঁদের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছে, তাঁরাই রাষ্ট্রের শাসক। রাষ্ট্রের শাসককে তৈরি করা হয়েছে মানুষের স্বাধীনতা, জীবন, সম্পত্তি রক্ষা তথা কল্যাণের জন্য। শাসক যদি অক্ষম, অযোগ্য ও জনকল্যাণে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার অধিকার জনগণের আছে।
(ii) আইনসভার ক্ষমতাচ্যুতি
লকের মতে, আইনসভাও চরম ক্ষমতার অধিকারী নয়। আইনসভা বা সরকার মানুষের আস্থা হারালে মানুষ আইনসভা বা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং নতুন চুক্তি সম্পাদন করার অধিকারী।
(iii) হস্তান্তরযোগ্য নয়
লকের মতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনপ্রণেতা তার ক্ষমতাকে অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছে হস্তান্তরিত করতে পারেন না। কারণ, জনগণ হল আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। যেহেতু জনগণ স্বেচ্ছায় এই ক্ষমতা আইনপ্রণেতার হাতে দিয়েছে, তাই আইনপ্রণেতা এই ক্ষমতা অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করতে পারেন না।
সরকার এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি
লকের মতে, রাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক – সরকার যে ধরনেরই হোক না কেন, তাকে সবসময় রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্দিষ্ট রীতিনীতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তিনি সরকার কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য ক্ষমতার পৃথকীকরণের পরামর্শ দিয়েছেন।
(i) আইন প্রণয়ন ও আইন কার্যকর করা
লক বলেছেন যে, আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা দুটি পৃথক কাজ। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে আইন বিভাগের হাতে এবং শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা থাকবে শাসন বিভাগের হাতে। লক মনে করেন যে, আইন রচনার কাজ স্বল্প সময়ে সমাপ্ত করা যায়। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আইন বিভাগের সদস্যদের নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মরত থাকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আইন কার্যকরী করার কাজটি সময়সাপেক্ষ কাজ, যার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। তাই এই দুটি কাজ দুটি স্বতন্ত্র বিভাগের হাতে থাকাই কাম্য। লক বলেছেন যে, প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের পথে মানুষের প্রথম কাজ হল আইন প্রণয়নী ক্ষমতা তৈরি করা। এটি যে-কোনো রাজনৈতিক সমাজেরই চূড়ান্ত ক্ষমতা (Supreme Power in every commonwealth)।
(ii) ফেডারেটিভ ক্ষমতা
বহির্দেশীয় কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য লক ফেডারেটিভ ক্ষমতার (Federative Power) কথা বলেছেন। এই ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি শাসকের বিচক্ষণতার উপর নির্ভরশীল। উদ্ভূত পরিস্থিতি, বিদেশি রাষ্ট্রের আচরণ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে শাসক এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে তিনি সম্মতি প্রদানকারী সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
সম্পত্তির অধিকার
জন লকের রাষ্ট্রতত্ত্বে সম্পত্তির অধিকার তত্ত্বটি (Theory of Property) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জন লক সম্পত্তির অধিকারকে বলেছেন রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
(i) সম্পত্তিতে সমানাধিকার
লক বলেছেন, প্রকৃতির সম্পদ সকল মানুষই সমানভাবে ভোগ করার অধিকারী। তবে কালক্রমে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
(ii) ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব
লকের মতে, যে সৃষ্টিকর্তা পার্থিব সম্পদ সমানভাবে ভোগ করার জন্য মানুষকে পাঠিয়েছেন, তিনিই মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন সেই সম্পদ ব্যবহার ও রক্ষার জন্য। মানুষ এই বুদ্ধির সঙ্গে কায়িক শ্রমকে মিশ্রিত করে যা অর্জন করে, সেটাই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। লক সম্পত্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি, তাঁর মতে এ বিষয়টি ব্যক্তির নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। তবে লক এও বলেছেন যে, অফুরন্ত সম্পত্তি অর্জন করা অন্যায় নয়, তবে তার একটি শর্ত আছে। সেই শর্তটি হল- ব্যক্তির সেই পরিমাণ সম্পত্তির উপরেই অধিকার থাকবে, যে পরিমাণ সম্পত্তি নষ্ট না করে সে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।
সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা
(iii) লক ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সরকারি
হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে বলেছেন, যে সরকার কর্তৃক সম্পত্তির প্রাকৃতিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, সেটি হল অবৈধ সরকার।
শ্রমতত্ত্ব
লকের রাষ্ট্রতত্ত্বে, ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগদখলের ক্ষেত্রে তার শ্রমের প্রসঙ্গটি তাৎপর্য সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির নিজ শ্রম
দ্বারা অর্জিত সম্পত্তির অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। লক শ্রম বলতে ব্যক্তির ক্ষমতা ও বাহুবলের কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, ব্যক্তির অধীনস্থ পশুশ্রম এবং ব্যক্তির অধীন ভূমিদাস শ্রেণির শ্রমও তার নিজস্ব শ্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। লকের শ্রমনির্ভর সম্পদ অর্জনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ তাঁকে কার্ল মার্কসের মূল্যতত্ত্বের পূর্বসূরি বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লক যেভাবে ভৃত্যের শ্রমকে মালিকেরই শ্রম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাতে তিনি তৎকালীন উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করতে চেয়েছিলেন বলেই মনে করা হয়ে থাকে।
বিরোধিতা ও বিপ্লব
জন লক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের বিরোধিতা করার অধিকারকে স্বীকার করেছেন। লকের টু ট্রিটিজস্ অফ গভর্নমেন্ট গ্রন্থের Book-II-এর The Dissolution of Government শীর্ষক অধ্যায়ে সরকারের বিলুপ্তি প্রসঙ্গে জনগণের ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে। লক সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বিপ্লব বা বিদ্রোহের কথা বলেননি। তাঁর মতে, শাসক বা সরকার যদি নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘন করে; অবিচার, শোষণ বা নির্বাচনের প্রতীক হিসেবে কাজ করে, তখন তার বিরোধিতা করা নাগরিকদের সহজাত অধিকার।
(i) অধিকাংশ মানুষের স্বার্থবিরোধী
বিরোধিতার বিষয়ে লক কোনও ব্যক্তিবিশেষের অধিকার বা ক্ষোভের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। যখন সরকার বা আইনসভার কাজ বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী হবে তখনই বিরোধিতার পথে এগোতে হবে।
(ii) স্বর্গের প্রতি আবেদন: অবশ্য লকের মতে, প্রথমে জনগণ আইন অনুযায়ী প্রতিবাদ জানাবে। এরপরও যদি সরকার নিজেই আইন লঙ্ঘন করে তখনই মানুষ বিরোধিতার পথ অবলম্বন করবে। এক্ষেত্রে লক Appeal to Heaven বা স্বর্গের প্রতি আবেদনের কথা বলেছেন। এখানে ‘Appeal to Heaven’ বলতে তিনি মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শক্তিকেই বুঝিয়েছেন।
আরও পড়ুন – মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা প্রশ্ন উত্তর