মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ প্রশ্ন উত্তর
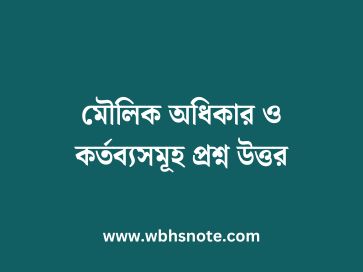
১। অধিকারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করো।
অধিকারের সংজ্ঞা: মানুষ সাধারণত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে চায়, আর সেইসঙ্গে চায় তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশ সাধন করতে। কিন্তু সুখী জীবনযাপন করার জন্য বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এমনি কিছু সুযোগসুবিধা মানুষের থাকা দরকার যেগুলি তার পক্ষে একান্ত ভাবেই অপরিহার্য। কারণ, সেগুলি ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী বাহ্যিক এই সুযোগসুবিধা গুলিই হল অধিকার। বি বোসাংকোয়েত এর ভাষায়, “অধিকার হল সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত দাবি”।
২। অধিকার সম্পর্কে অধ্যাপক ল্যাঙ্কির মত ব্যক্ত করো।
অধিকার সম্পর্কে ল্যাস্কি-র মত: অধ্যাপক ল্যাস্কি-এর মতে, অধিকার হল সমাজজীবনের সেইসব সুযোগসুবিধা, যেগুলি ছাড়া কোনো ব্যক্তি সাধারণভাবে তার ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটাতে পারে না। তাঁর মতে, রাষ্ট্র নাগরিককে কী পরিমাণ অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, তার উপরে নির্ভর করবে সে কতখানি আনুগত্য তাদের কাছে দাবি করতে পারবে। সুতরাং রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে স্বীকার ও সংরক্ষণ করে মাত্র।
৩। অ্যারিস্টটলের মতানুসারে, অধিকার কী?
অধিকার সম্পর্কে অ্যারিস্টট্ল-এর মত: গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষ হল প্রকৃতিগতভাবে সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ যে সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করে সেগুলিকে অধিকার বলে। অধিকার কোনো নেতিবাচক ধারনা নয়।
তিনি আরও বলেন যে, সুন্দর জীবনের জন্য অবকাশ অপরিহার্য। সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অবকাশের অধিকার একান্ত প্রয়োজন। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন অবকাশের।
৪। অধিকার সম্পর্কে আর্নেস্ট বার্কার-এর সংজ্ঞা দাও।
অধিকার সম্পর্কে আর্নেস্ট বার্কার এর মত: বার্কার-এর মতে, অধিকার হল যথাসম্ভব সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সর্বাধিক পরিমাণ সেইসব বাহ্যিক সুযোগসুবিধা, যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।
বার্কার এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী দুটি শর্ত পূরণ করলে কোনো সুযোগসুবিধাকে অধিকার বলে অভিহিত করা যেতে পারে, সুযোগ- – সুবিধাগুলি প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে। সুযোগসুবিধাগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হবে।
৫। অধিকার সম্পর্কে টি এইচ গ্রিণ এর মত ব্যাখ্যা করো।
অধিকার সম্পর্কে টি এইচ গ্রিন-এর মত: গ্রিন-এর মতে,- “পরস্পরের প্রয়োজন সম্পর্কে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সমাজ ছাড়া অধিকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না”। ব্যক্তির কেবল নিজের সুখসুবিধার কথা ভাবলেই চলবে না, সেই সঙ্গে অপরের সুখসুবিধার কথাও চিন্তা করতে হবে। যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সুযোগসুবিধার সঙ্গে অপরের সুযোগসুবিধার কথাও চিন্তা করবে, তখনই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।
৬। অধিকার সম্পর্কে গিলক্রিস্ট এবং হবহাউস এর অভিমত সংক্ষেপে লেখো।
অধিকার সম্পর্কে গিলক্রিস্ট-এর মত: গিলক্রিস্ট মনে করেন, অধিকার হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত সেইসব সুযোগসুবিধা যার সাহায্যে ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।
অধিকার সম্পর্কে হবহাউস-এর মত: হবহাউস-এর মতে, আমরা একে অপরের থেকে যা প্রত্যাশা করি, সেটাই অধিকার। অধিকারের পশ্চাতে সামাজিক অনুমোদন থাকে।
৭। অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
অধিকারের বৈশিষ্ট্য সমূহ: অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল, ব্যক্তি শুধুমাত্র সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে অধিকার ভোগ করতে পারে। সমাজের বাইরে অধিকারের কোনো অস্তিত্ব নেই। অধিকারের একটি আইনগত দিক আছে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদনের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
৮। অধিকারের রূপ বা প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অধিকারের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাভেদ: অধিকারকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যথা- নৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকার, আবার এই আইনগত অধিকারগুলিকে প্রকৃতি অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা যায় যথা- পৌর অধিকার, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক ও কৃষ্টিগত অধিকার।
৯। নৈতিক অধিকার কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
নৈতিক অধিকার: যেসব অধিকার সামাজিক ন্যায়নীতি বোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাদের নৈতিক অধিকার (Moral Rights) বলা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শুধুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করেন এবং সমাজের কাছে নিন্দিত হন মাত্র।
উদাহরণ: যেমন-বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তানের কাছে ভরণপোষণ পাওয়ার নৈতিক অধিকার পিতামাতার রয়েছে, কিন্তু কোনো সন্তানের আচরণে এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিছু করার থাকে না। কাজেই নৈতিক অধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত নয়।
১০। আইনগত অধিকার কাকে বলে? এটি কয় প্রকার এবং কী কী?
আইনগত অধিকার: অন্যদিকে যেসব অধিকার আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয়, তাদের আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলে। আইনগত অধিকার লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে। যেমন, ভোটদান করার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। এই অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে, রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে।
প্রকারভেদ: পৌর অধিকার (Civil Rights), রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights), অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) এবং সামাজিক ও কৃষ্টিগত অধিকার (Social and Cultural Rights) I
১১। পৌর অধিকার কাকে বলে? এটি কতপ্রকার এবং কী কী?
পৌর অধিকার: যেসকল সুযোগসুবিধা ব্যতীত মানুষের পক্ষে সভ্য সামাজিক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়, তাকে পৌর অধিকার (Civil Rights) বলে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পৌর অধিকার একান্তভাবে অপরিহার্য। নিম্নলিখিত পৌর অধিকারসমূহ সভ্য সমাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
প্রকারভেদ: পৌর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অধিকারগুলি হল- জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার।
১২। রাজনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝো? এর প্রকারভেদ সংক্ষেপে লেখো।
রাজনৈতিক অধিকার: রাষ্ট্রের কোনো কাজকর্মে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগসুবিধাকে রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) বলা হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রকারভেদ: রাজনৈতিক অধিকারগুলি হল- ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার, সরকারি চাকুরিতে আবেদন করার অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার, বিদেশে থাকাকালীন নিরাপত্তার অধিকার, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার।
১৩। অর্থনৈতিক অধিকার কাকে বলে? এটি কয় প্রকার ও কী কী?
অর্থনৈতিক অধিকার: অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) ছাড়া পৌর, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলি নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই অর্থনৈতিক অধিকারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অর্থনৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেই সকল অধিকারকে বুঝি, যেগুলি মানুষকে দারিদ্র্যতা এবং অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ করে গড়ে তোলে। অধ্যাপক ল্যাস্কি-র মতে, প্রাত্যহিক অন্নসংস্থানের ক্ষেত্রে মানুষের ন্যায়সংগত মজুরি পাওয়ার নিরাপত্তা ও সুযোগকে অর্থনৈতিক অধিকার বলা যায়। বার্কার আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যে শ্রমিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন, সে কখনোই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হতে পারে না।
উদাহরণ: অর্থনৈতিক অধিকার গুলি হল— কর্মের অধিকার, যথাযথ পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, বার্ধক্য ও অক্ষম অবস্থায় প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার।
১৪। সামাজিক অধিকার কাকে বলে? এটি কয় প্রকার এবং কী কী?
সামাজিক ও কৃষ্টিগত অধিকার: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের জন্য যেসব সুযোগসুবিধা একান্তভাবে অপরিহার্য, তাকে সামাজিক ও কৃষ্টিগত অধিকার (Social and Cultural Rights) বলা হয়।
প্রকারভেদ: আধুনিক যুগে জনকল্যাণকামী বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেসব সামাজিক ও কৃষ্টিগত অধিকার উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল- সামাজিক সুস্থ পরিবেশে বাস করার অধিকার, স্বাস্থ্য সাম্যের অধিকার, রক্ষার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার।
১৫। যে কোনো দুটি পৌর অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
জীবনের অধিকার: মৌলিক পৌর অধিকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবনের অধিকারকে অনেকসময় সহজাত অধিকার হিসেবেও ধরা হয়। এই অধিকার অনুযায়ী উপযুক্ত আইনসম্মত পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির প্রাণনাশ করা যায় না, যদি তা করা হয় তবে সেটি আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।
স্বাধীনতার অধিকার: জীবনকে উপভোগ করার জন্য স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োজন। রাষ্ট্র অযথা ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে স্বাধীনতার অধিকারের যাতে অপব্যাবহার না ঘটে, সেদিকে সরকার ও জনগণের সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।
১৬। যে-কোনো দুটি রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
ভোটদানের অধিকার: ভোটদানের অধিকার ছাড়া রাষ্ট্র ও সরকারের সঙ্গে জনগণের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে না। কারণ, একমাত্র স্বাধীন এবং অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই জনগণ তাদের পছন্দমতো প্রতিনিধি নির্বাচন করে রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
সরকারি চাকুরিতে অংশগ্রহণের অধিকার: রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল- সরকারি চাকুরিতে অংশ গ্রহণের অধিকার। এর মাধ্যমে নাগরিকরা যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত হওয়ায় সুযোগ লাভ করে।
১৭। যে-কোনো দুটি অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
কর্মের অধিকার: অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে প্রথমেই কর্মের অধিকারের উল্লেখ করা যায়। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের কর্মের সুযোগ থাকা দরকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা এবং প্রবণতা অনুযায়ী কর্ম নির্বাচন করার সুযোগসুবিধা এইরূপ অধিকারেরই অঙ্গ।
কর্মের উপযোগী বেতন লাভের অধিকার: কর্মে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির বেতন বা বেতনক্রম এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তার ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানকে সুনিশ্চিত করা যায়। যদি তা না হয় তাহলে মানুষ তার উপরি-উপার্জনকে বেছে নিতে পারে। এতে রাষ্ট্রের এবং পক্ষান্তরে সমগ্র জনগণেরই ক্ষতি হতে পারে।
১৮। যে-কোনো দুটি সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
শিক্ষার অধিকার: সামাজিক অধিকারগুলি হল সমষ্টিগত অধিকার। এই অধিকারের মধ্যে প্রথমেই শিক্ষার অধিকার স্থান পেয়েছে। ল্যাস্কি বলেন, শিক্ষার অধিকার নাগরিকদের জ্ঞানপ্রসূত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে সাহায্য করে। নিজের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার অধিকার মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
সাংস্কৃতিক অধিকার: কোনো মানুষ, দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশ একমাত্র শিক্ষার উন্নতির উপরেই নির্ভরশীল। তা ছাড়া খেলাধুলা, নাটক, সংগীত প্রভৃতিতে নাগরিকদের স্বাধীন অংশগ্রহণের প্রশ্নটিও সাংস্কৃতিক অধিকাররূপে পরিচিত।
১৯। অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি কী কী?
অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ: অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব, আইনগত তত্ত্ব, আদর্শবাদী তত্ত্ব, মার্কসীয় তত্ত্ব।
২০। স্বাভাবিক অধিকার বিষয়ক তত্ত্ব বলতে কী বোঝো? এই তত্ত্বের মূল তাত্ত্বিকদের নাম লেখো।
স্বাভাবিক অধিকার বিষয়ক তত্ত্ব: যেসব অধিকার মানুষের সহজাত, যে অধিকারগুলি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেগুলি হল স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার গুলি সর্বজনীন ও চিরন্তন। রাষ্ট্র বা সমাজ নয়, প্রাক্-সামাজিক ও প্রাক্-রাজনৈতিক বিষয় এই অধিকারের উৎস। এই কারণে রাষ্ট্র স্বাভাবিক অধিকারের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না।
তাত্ত্বিকগণ: প্রাচীন গ্রিসের স্টোয়িক দর্শনে এবং রোমান আইনবিদদের লেখায় স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস হক্স, জন লক্ এবং জ্যাঁ জ্যাক রুশোর রচনায় স্বাভাবিক অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে স্পেনসার, গিডিংস, বেত্থাম, গ্রিন ও ল্যাস্কির লেখাতেও এই তত্ত্বটি সমর্থিত হয়।
২১। অধিকারের আইনগত তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো। এই তত্ত্বের মূল তাত্ত্বিকদের নাম লেখো।
অধিকারের আইনগত তত্ত্ব: অধিকারের আইনগত তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, রাষ্ট্রবহির্ভূত কোনোরকম অধিকারের অস্তিত্ব বাস্তবে থাকতে পারে না। যাবতীয় অধিকারের উৎস হল রাষ্ট্র। ব্যোম-এর মতে, অধিকার হল আইনের সন্তান। আইনগত মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, রাষ্ট্রের একটি মৌলিক আইনগত কাঠামো আছে, যার সাহায্যে অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের কাজ করা হয়। বস্তুত, আইনের মাধ্যমে অধিকারের সৃষ্টি হয় বলে আইনের রদবদলের সঙ্গে অধিকারেরও রদবদল ঘটে। অধিকারের আইনগত তত্ত্বের প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, অধিকার ভোগের জন্য নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো বাধ্যতামূলক।
তাত্ত্বিকগণ: বেথাম, অস্টিন, সলমন্ড, রিচি প্রমুখ হলেন অধিকারের আইনগত তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা।
২২। অধিকারের আদর্শবাদী তত্ত্ব বলতে কী বোঝো? এই তত্ত্বের সমর্থক চিন্তাবিদদের নাম উল্লেখ করো।
আদর্শবাদী তত্ত্ব: অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান আদর্শবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে তত্ত্বের অবতারণা করেন, তা থেকেই অধিকারের আদর্শবাদী তত্ত্বের জন্ম হয়।
অধিকারের আদর্শবাদী তত্ত্বের মূল বক্তব্য অনুসারে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য বাহ্যিক শর্তগুলি হল অধিকার। আদর্শবাদী দার্শনিকরা অধিকার ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যপালনের বিষয়টিকেও যুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, একজন ব্যক্তির অধিকার ভোগের বিষয়টি তার কর্তব্যপালনের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষ। আদর্শবাদী দার্শনিকরা স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, সমাজ বা রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোনো অধিকার বাস্তবে থাকতে পারে না। রাষ্ট্র একটি অখন্ড সামগ্রিক সত্তা, ব্যক্তি তার অংশমাত্র।
তাত্ত্বিকগণ: জার্মান আদর্শবাদী দার্শনিক কান্ট এবং ইংরেজ দার্শনিক গ্রিন ব্যক্তির অধিকারকে নৈতিক মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই মতবাদের অবতারণা করেছেন। কান্ট-এর মতে, নৈতিক দিক থেকে স্বাধীন ব্যক্তিকে প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি বলা যেতে পারে। গ্রিন-এর মতে, ব্যক্তির দাবি যখন সর্বজনীন কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত হয়, তখন তাকে প্রকৃত অধিকার বলা যেতে পারে।
২৩। অধিকার সম্পর্কে মার্কসবাদীদের অভিমত ব্যাখা করো।
অধিকার সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা: মার্কসবাদ অধিকারকে কোনো বিমূর্ত বা কাল্পনিক ধারণা বলে মনে করে না। মার্কসবাদীদের ধারণা হল, সমাজের শ্রেণিকাঠামো এবং সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে অধিকারের ধারণা জড়িত রয়েছে। তবে মার্কসবাদীরা মনে করেন, বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থায় অধিকার সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে না। তাই শ্রেণিশাসিত ও শোষণমূলক সমাজে অধিকারের ধারণাটি বৈষম্যমূলক। উৎপাদনের উপাদান যেখানে সংখ্যালঘুর হাতে কেন্দ্রীভূত, অর্থনৈতিক অসাম্য যে ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শোষকের স্বার্থেই অধিকারের ধারণাটি গড়ে ওঠে। তাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই জনগণের প্রকৃত অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হতে পারে।
২৪। কর্তব্য কাকে বলে?
কর্তব্যের সংজ্ঞা: কর্তব্য বলতে কোনো কিছুর প্রতি দায়িত্ব পালন করাকে বোঝায়। যেমন-দেশের অভ্যন্তরে আইন মেনে চলা একটি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। অধিকার তখনই ভোগ করা যায়, যখন তার পূর্বে কোনো কর্তব্য পালন করা হয়। একইভাবে জনগণের কাছ থেকে রাষ্ট্র কিছু কর্তব্য আশা করে থাকে। একজন ব্যক্তির চেতনা (Civic Sense) জাগ্রত হওয়ার উপরে অন্য ব্যক্তিদের অধিকারভোগ ও কর্তব্য পালনের বিষয়টি নির্ভর করে চলে। বিভিন্ন দেশ, যেমন-ভারত, চিন ও জাপানের সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।
২৫। ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?
ব্যাপক অর্থে কর্তব্য: ব্যাপক অর্থে বা ইতিবাচক অর্থে কর্তব্যকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি হল নৈতিক কর্তব্য, যা মূলত ব্যক্তির বিবেকবোধ ও ন্যায়-অন্যায়বোধ থেকে তৈরি হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো বলপূর্বক আইন প্রয়োগ করে না। যেমন, অনাথ শিশুদের প্রতি ভালোবাসা, বৃদ্ধ পিতামাতার যত্ন নেওয়া ইত্যাদি। অপরটি আইনগত কর্তব্য, অর্থাৎ যেখানে রাষ্ট্র ও সরকারের মহৎ কোনো লক্ষ্যপূরণে বা দেশরক্ষার কার্যে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সুষ্ঠুভাবে ভোটদান ইত্যাদিকে বোঝায়।
সংকীর্ণ অর্থে কর্তব্য: কোনো ব্যক্তি যদি অপরের জীবনহানি করে থাকে, নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য সেবন বা পাচার-সহ জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করে থাকে, তবে সেগুলি নেতিবাচক বা সংকীর্ণ কর্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র এহেন ক্রিয়াকলাপ থেকে নাগরিকদের বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। প্রয়োজনে তা গুরুতর অপরাধ বলেও গণ্য হয় ও বিচারে ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পর্যন্ত হয়।
২৬। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের বলবৎযোগ্যতা স্থগিত রাখা যায়?
অথবা, জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকারের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা যায় কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দাও।
জরুরি অবস্থায় অবলবৎযোগ্য: স্বাভাবিক অবস্থায় মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিকরা আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তার প্রতিকার চাইতে পারে কিন্তু জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায় না। দেশে যখন জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়, তখন রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫৯ নং ধারা অনুযায়ী আদেশ জারি করে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করার অধিকারকে বাতিল করে দিতে পারেন। তবে সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধনের (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, জরুরি অবস্থার কালেও রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ২১ নং ধারায় উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখতে পারবেন না।
২৭। মৌলিক অধিকার গুলি কী নিরঙ্কুশ?
ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি ব্যক্তির পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের এক অপরিহার্য শর্ত। মৌলিক অধিকারগুলি ব্যক্তিকে তার অধিকার সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। তবে একথা অবশ্যই বলা যায়, মৌলিক অধিকারগুলি কখনোই অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ অধিকার যদি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে সেই অধিকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে। তাই বলা যায়, সকলের জন্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে মৌলিক অধিকারগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজনীয়। তাই সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির উপর কিছু যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
২৮। শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য উল্লিখিত দুটি মৌলিক অধিকার লেখো।
শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ:
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান ভেদে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না (১৫ নং ধারা)।
- সরকারি চাকুরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সমান সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকার (১৬ নং ধারা)
- ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার যথা- বাস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ করার অধিকার, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, সংঘ বা সমিতি কিংবা সমবায় সমিতি গঠনের অধিকার, ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করার অধিকার, ভারতের যে-কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার এবং যে-কোনো বৃত্তি, পেশা বা ব্যাবসাবাণিজ্য করার অধিকার। (১৯ নং ধারা)।
২৯। কোন্ কোন্ অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা যায় না?
ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যেসব মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা যায়। উদাহরণ হিসেবে অস্পৃশ্যতা বর্জন (১৭ নং ধারা) কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ না করার (১৮ নং ধরা) কথা বলা হয়েছে।
৩০। কত তম সংবিধান-সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা হারায়? কত সালে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা হারিয়েছে?
৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা হারায়।
১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ক্ষমতাসীন জনতা দল কর্তৃক ৪৪তম সংবিধান সংশোধন পাশ হয়। এই সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা হারায়।
৩১। মৌলিক অধিকারগুলি কি সংশোধনযোগ্য?
মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধনযোগ্য: ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের জন্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। এগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধনযোগ্য। তবে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলিকে সংশোধন করতে গেলে সংবিধান সংশোধন করতে হয়। সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই- তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলি সংশোধন করা যায়।
৩২। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উপর মৌলিক অধিকারভোগের ক্ষেত্রে কী বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়?
সামরিক বাহিনী, জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত অন্যান্য বাহিনীর যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন সুনিশ্চিত করার জন্য এইসব বাহিনীর সদস্যরা কতখানি মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে তা পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে স্থির করে দিতে পারে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানের ৫০তম সংশোধনের মাধ্যমে গোয়েন্দা ব্যুরো, সরকারি সম্পত্তির রক্ষী বাহিনীর সদস্য, গোয়েন্দা বিভাগ বা এ ধরনের সংস্থার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রেও সংবিধানের বিধান প্রযুক্ত হবে।
৩৩। সরকারি চাকরিতেসম সুযোগের একটি ব্যতিক্রম লেখো।
ব্যতিক্রম: সরকারি চাকুরিতে সমসুযোগের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল-
রাষ্ট্র তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সরকারি চাকরিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। বর্তমানে শতকরা ১৫ ভাগ সর্বভারতীয় চাকরি তপশিলি জাতির জন্য এবং ৭১ ভাগ তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সরকারি চাকরিতে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার।
৩৪। আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি বলতে কী বোঝ?
আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি: ‘আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি’ অনুযায়ী আদালত কোনো আইন ন্যায়নীতিবোধ বিরোধী কি না অর্থাৎ আইনের গুণাগুণ, তা বিচার করতে পারে না। আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি বলতে বোঝায়, যে আইন অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হবে সেই আইনটি বিধিসম্মতভাবে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কি না তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকবে। বলা যায়, ভারতীয় সংবিধান বিচারবিভাগের প্রাধান্যের পরিবর্তে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতাকেই স্বীকার করে নিয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না তা দেখার ক্ষমতা আদালতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।
আরও পড়ুন – মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা প্রশ্ন উত্তর