জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে উত্তরণ কীভাবে হয়েছিল
অথবা, জ্যোতিষশাস্ত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার ভিত্তিভূমি বলা হয়ে থাকে- তোমার অভিমত কী
অথবা, ‘জ্যোতিষচর্চা (Astrology) জ্যোতির্বিজ্ঞানের (Astronomy) পথের দিশারী-তুমি কি ইহা সমর্থন করো অথবা, জ্যোতিষশাস্ত্রের ঐতিহ্যগত ধারণা সংক্ষেপে আলোচনা করো
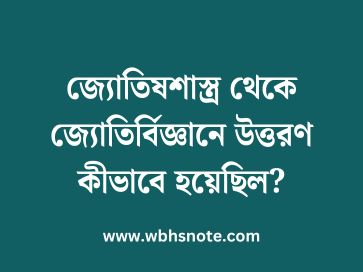
জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রায় সমোচ্চারিত এই শব্দ দুটিকে আপাত এক বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশেষ অর্থবহ। জ্যোতিষবিদ্যা বা জ্যোতিষচর্চার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Astrology. আর জ্যোতিবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Astronomy.
জ্যোতিষশাস্ত্রের ধারণা
সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশের গ্রহনক্ষত্র বিষয়ক আলোচনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। গ্রিক শব্দ Astron অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলী এবং Logia অর্থাৎ অধ্যয়ন বা বিদ্যা শব্দের সমন্বয়ে Astrology বা জ্যোতিষবিদ্যা শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। এই জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মীয় ধ্যানধারণার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।
জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা
জ্যোতির্বিদ্যা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। এখানে মহাবিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে চর্চা করা হয়। অর্থাৎ, জ্যোতির্বিদ্যা একপ্রকার ধর্মনিরপেক্ষ ও নিরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান। এই কারণে জ্যোতির্বিদ্যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা Astronomy কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ Astro (নক্ষত্র) এবং Nomos (আইন বা সংস্কৃতি) থেকে। ‘Astronomy’ কথার অর্থ হল- নক্ষত্রসমূহের বিন্যাস। বলা হয়, প্রাচীন কালে গ্রিসে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা Astronomy-এর প্রচলন ছিল। স্বয়ং প্লেটো নাকি জ্যোতির্বিজ্ঞান বা Astronomy কথার বদলে জ্যোতিষশাস্ত্র বা Astrology শব্দটির প্রবর্তন করেন।
জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে উত্তরণ
জ্যোতিষশাস্ত্র মূলত ধর্মভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল চালিকাশক্তি হল নিরন্তর পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক বিচার দ্বারা পর্যবেক্ষণের শিক্ষাকে যুক্তিসিদ্ধ করা। উভয়ক্ষেত্রেই গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান ও মানবসমাজের উপর তার প্রভাব হল প্রধান আলোচ্য বিষয়। শুরুতে জ্যোতির্বিদরা পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বব্র্যান্ডের কথা বললেও, ক্রমেই এই ধারণায় নানা পরিবর্তন আসতে থাকে। ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটালে এই ধারণায় ঘটে আমূল পরিবর্তন।
(1) অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব: অ্যারিস্টটলের এক বিখ্যাত তত্ত্ব হল ‘দুই বিশ্বের তত্ত্ব’ -যেখানে তিনি বিশুদ্ধ স্বর্গ ও অশুদ্ধ মর্ত্যের কথা তুলে ধরেন। তাঁর তত্ত্ব থেকে এমন একটি অস্পষ্ট ধারণা উঠে আসে যে, সমগ্র বিশ্ব কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন এবং এই প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ধর্মের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। যদিও তিনি মহাকাশের কেন্দ্রে পৃথিবীর অবস্থানকে স্বীকার করে নেন, কিন্তু তবু তাঁর অভিমত খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সংশয় সৃষ্টি করে। পৃথিবীকে যে দৈবশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে- এরূপ ধারণার ভিত্তি কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। অ্যারিস্টটলের এরূপ সংশয়বাদী সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিশার সন্ধান দেয়।
(2) বল্লান্ড তত্ত্ব ব্যাখ্যায় টলেমি: টলেমি পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদদের অনুসরণ করে তাঁর পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন অ্যালমাজেস্ট গ্রন্থে। তিনি বিশ্বাস করতেন- বিশ্বব্র্যান্ডের কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত এবং তা স্থির। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগুলি পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। তাঁর এই তত্ত্ব Ptolemaic System বা ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব নামে পরিচিত। টলেমির ভূকেন্দ্রিক বিষয়ক এই ধারণা বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত টলেমির তত্ত্ব প্রায় সমগ্র খ্রিস্টান জগতে ছিল গ্রহণযোগ্য। তবে এরই পাশাপাশি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গতি, পৃথিবীর আহ্নিক গতি ইত্যাদি বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনা ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কাজকে অনেকটাই এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।
(3) পিথাগোরাসের অনুগামীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া: টলেমির তত্ত্ব প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রিক জ্যোতিষশাস্ত্রবিদরা, যেমন- পিথাগোরাসের অনুগামীরা তাঁর তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের মতে, সূর্যই স্থির। এই তত্ত্ব ‘Heliocentric Theory’ নামে পরিচিত। ধ্রুপদি সভ্যতার পুনরাবিষ্কার এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রিক অধ্যয়নের পুনর্জাগরণের ফলে পিথাগোরাসের তত্ত্ব ক্রমশ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে এবং সকলেই সেই – তত্ত্বকে গুরুত্ব দিতে থাকেন।
(4) অ্যারিস্টারকাসের তত্ত্ব: এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী দ্বীপ সামোস-এর বাসিন্দা অ্যারিস্টারকাস (Aristarchus of Samos) ব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রে সূর্যের অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পাশাপাশি পৃথিবী নিজেও লাটুর মতো ঘুরছে। তিনি বলেন, সূর্যের আকৃতি, চাঁদের আকৃতির ১৯ গুণ বেশি এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের ১৯ গুণ। যদিও এই হিসাব বর্তমানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। চাঁদের আকারের তুলনায় সূর্যের আকার ৪০০ গুণ বড়ো এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, চাঁদের দূরত্বের ৩৯০ গুণ। তবে এটাও ঘটনা যে, হিসাব ভুল হলেও, আকৃতির এই তুলনামূলক আলোচনার জন্যই অ্যারিস্টারকাস বুঝতে পেরেছিলেন যে, দূর থেকে ছোটো দেখালেও সূর্য পৃথিবীর তুলনায় অনেকগুণই বড়ো।
(5) কোপারনিকাসের চন্দ্র: জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ষোড়শ শতকে ঘটে যায় এক বিপ্লব। এসময় কোপারনিকাস ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের বদলে তুলে ধরেন সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের ছবি। কোপারনিকাস তাঁর ‘On the Revolutions of the Heavenly Spheres’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বব্র্যান্ডের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী নয়, সূর্যই স্থির। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহ, উপগ্রহগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমা করছে। কোপারনিকাসের এই তত্ত্ব ছিল প্রচলিত ধারণার বিরোধী।
মূল্যায়ন
এভাবেই জ্যোতির্বিদরা জ্যোতিষচর্চা করতে গিয়ে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষ সহায়ক হয়। কোপারনিকাস তাঁর সৌরতত্ত্বকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। পরবর্তীকালে জিওরদানো ব্রুনো, টাইকো ব্রাহে, জোহানেস কেপলার, গ্যালিলিও প্রমুখেরা সেই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দানের মাধ্যমে খুলে দিয়েছিলেন আধুনিক জ্ঞানের দ্বার, বিমুক্তি ঘটেছিল সত্যের। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনগড়া তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব তত্ত্ব। তাই ‘জ্যোতিষচর্চা যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথের দিশারী’ -একথা নিঃসেন্দেহে সমর্থনযোগ্য।
আরও পড়ুন – মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা প্রশ্ন উত্তর