অশ্বারোহণ বলতে কী বোঝো? বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার অবদান আলোচনা করো
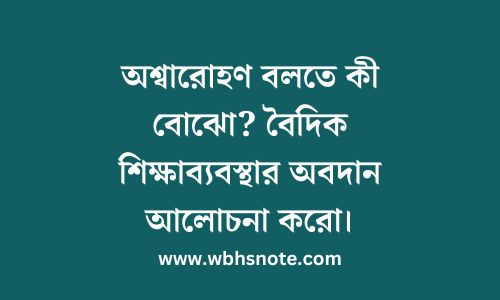
অশ্বারোহণ
বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করে অভিষেক হওয়ার পর আরও একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত, তাকে বলা হত অশ্বারোহণ। শিক্ষাজীবনে এক নিষ্ঠাবান প্রতীকরূপে ব্রহ্মচারীকে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড় করানো হত। শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষার্থীদের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও অপরাজেয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই অনুষ্ঠান পালিত হত।
বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার অবদান
(1) ব্যস্তিত্বের বিকাশ: বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হত। ন্যায়, সততা, শ্রদ্ধাশীলতা, আদর্শপরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মনুষ্যরূপে গড়ে তোলাই ছিল এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।
(2) চাহিদাভিত্তিক: এই শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু প্রতিটি শিষ্যকে তার ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন।
(3) আত্মনিয়ন্ত্রণ: বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে কঠোর শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করতে হত। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মসংযমী হত। আত্মসংযমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করত।
(4) নারীশিক্ষা: বৈদিক সমাজে নারীর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে, তারা পুরুষদের সঙ্গে সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত। এমনকি শিক্ষাগ্রহণেও এদের সম অধিকার ছিল। এই যুগে ঋষি নারীকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হত।
(5) স্বাধীনতা: আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় আচার্যগণ পাঠ্যসূচি নির্বাচন, শিক্ষাদান, পরীক্ষা পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত।
(6) শৃঙ্খলা: বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভর, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ হত। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার এই শৃঙ্খলা নীতি আধুনিক কালে অনুসরণযোগ্য
(7) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানদের বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হত। তবে শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের কোনো বেতন দিতে হত না। ফলে ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেত।
(8) ‘সর্দার পাড়া’-প্রথার উদ্ভব : বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ পদ্ধতি হল এখানে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ছাত্ররা নিম্নশ্রেণির ছাত্রদের শিক্ষা দান করত। এই ব্যবস্থা থেকে পরবর্তীকালে সর্দার পড়ো প্রথা চালু হয়েছে। এর ফলে নবীন-প্রবীণ উভয় শ্রেণির ছাত্ররা বিশেষ উপকৃত হত।
(9) সু-ভাভ্যাস গঠন: গুরুগৃহে সংযমী জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি সু-অভ্যাস গঠনের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হত, যা বর্তমান দিনে খুবই প্রয়োজনীয়।
(10) সু-নাগরিকতার প্রশিক্ষণ: ‘পরাবিদ্যা’ ও ‘অপরাবিদ্যা’-র সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আদর্শ নাগরিকতার প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল এই যুগের > শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, যা আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য বিশেষ জরুরি।
(11) গুরু -শিষ্যের সম্পর্ক : এই শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের ন্যায় অত্যন্ত মধুর। শিষ্য গুরুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করত আর গুরু পিতার ন্যায় শিষ্যের সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করতেন। হয়তো এই আদর্শকে সামনে রেখে বর্তমান শিক্ষকের দায়িত্ব পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক।
(12) প্রকৃতির মানারম পরিবেশে শিক্ষাদান: প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষকের সুশীতল ছায়ায় শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। এই আদর্শকে সামনে রেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 1911 সালে শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ গঠন করেছিলেন।
(13) ব্যস্তিমুখী শিক্ষার প্রবর্তন: বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু প্রত্যেক শিষ্যকে তার নিজের চাহিদা, সামর্থ্য, প্রবণতা, বুচি প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদান করতেন। ফলে সব শিষ্যই প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানলাভ করতে পারত।
(14) আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা: বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের গৃহে থেকে শিক্ষালাভ করতে হত। এই আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের যেমন বিকাশ ঘটত, তেমনই তাদের মনে প্রতিযোগী মনোভাবের সৃষ্টি হত, যা পঠনপাঠনে আরও আগ্রহী করে তুলত।
আরও পড়ুন – বিকাশের স্তরসমূহ প্রশ্ন উত্তর